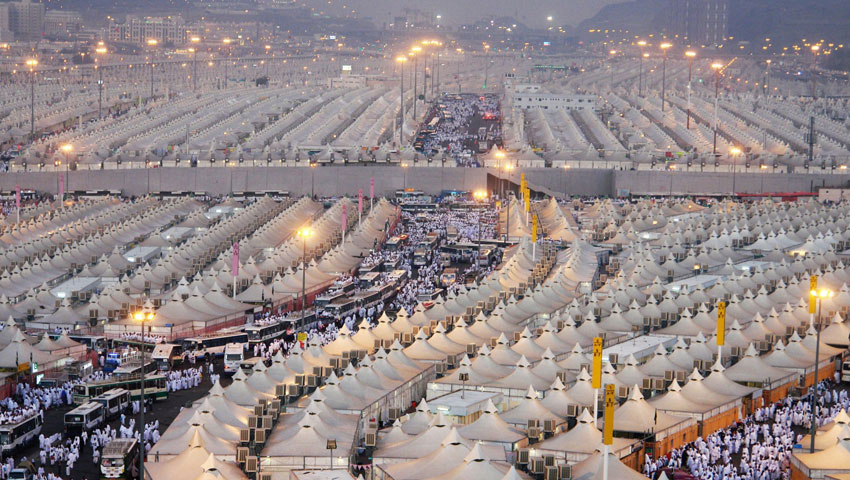সীতাকুণ্ডের সলিমপুর এলাকার বাবুল হক। চাকরির কারণে সোদিআরব থাকেন দীর্ঘদিন। ২৯ এপ্রিলের ভয়াল রাতে তিনি হারান তার মা-বাবাসহ পরিবারের ৫ সদস্যকে। বিদেশ থাকার কারণে সে বেঁচে যায় । তিনি এখনও বয়ে বেড়ান সেই স্মৃতি।
তিনি বলেন, আমরা ১০ নং মহাবিপদ সংকেত শুনলেও তেমন গুরুত্ব দিইনি। মুহূর্তের মধ্যে পানির থাবায় সব এলোমেলো হয়ে যায়। আমার পাকা ঘরের নিচে চাপা পড়েন সবাই। আমি বাইরে থাকায় হয়তো সেদিন বেঁচে যাই।
১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল ভয়াল সেই রাতের ঘটনার ৩৪ বছর পার হয়েছে। এখনো স্বজনের অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছেন ঘূর্ণিঝড়ে পাতিলে ভেসে আসা ৩৬ বছর বয়সী যুবক মুসলিম উদ্দিন। বর্তমানে তিন মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে বাস করছেন সীতাকুণ্ডের ভাটিয়ারী ইউনিয়নের জঙ্গল ভাটিয়ারী পাহাড়ের ভেতরে স্থাপিত আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরে। প্রতিবছর এই দিন এলে স্বজন হারানোর বেদনায় ডুকরে কেঁদে ওঠেন তিনি। অশ্রুতে বুক ভাসালেও তিনি এখনো জানেন না তাঁর মা-বাবা কে কিংবা তাঁদের বাড়িঘর কোথায় ছিল।
অশ্রুসিক্ত মুসলিম জানান, ঘূর্ণিঝড়ের সময় তিনি দুই বছরের শিশু। তিনি বড় একটি পাতিলের ভেতরে করে ভেসে ভাটিয়ারী উপকূলে আসেন বলে স্থানীয়দের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। ঘূর্ণিঝড়ের পরদিন ভেসে আসা পাতিলের ভেতর থেকে কান্নার শব্দ শুনে জেলে সম্প্রদায়ের এক লোক তাঁকে উদ্ধার করেন। পরে তাঁকে ভাটিয়ারী বাজারের উত্তর পাশের তেলীবাড়ী এলাকার স্থানীয় এক মুসলিম পরিবারের কোলে তুলে দেন।
শিশুকালের সেই সময়ের স্মৃতি তাঁর মনে না থাকলেও ৭ থেকে ৮ বছর বয়সের স্মৃতি তাঁর বেশ মনে রয়েছে। আট বছর বয়সে যখন তাঁর পালক বাবার পরিবারে অভাব-অনটন দেখা দেয়। তখন তিনি ভাটিয়ারী কাঁচাবাজারে ঘুরে ঘুরে পলিথিন (বাজারের ব্যাগ) বিক্রি শুরু করেন। পরে নিজের চেষ্টায় উঠে দাঁড়িয়েছেন।
মুসলিম উদ্দিন আরও জানান, তিন মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে বর্তমানে সুখের সংসার করলেও নিজের পিতৃপরিচয়ের শূন্যতায় নীরবে কাঁদছেন তিনি। বর্তমানে তাঁর মা-বাবা কোথায় আছেন, কেমন আছেন, জানেন না তিনি। তাঁদের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, এটাই সবচেয়ে বড় কষ্টের অনুভূতি তাঁর জীবনে।
আবদুল হালিম । বাড়ি বাঁশখালী। ১৯৯১ সালের ভয়াল সেই ২৯ এপ্রিল রাতে তিনি হারিয়েছেন পিতা-মাতাসহ পরিবারের ১১ জন। তিনি জানান, ঘূর্ণিঝড়ে আমার পরিবারের ১১ সদস্যকে আমি হারিয়েছি। আমার পরিবারে আমি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। তাই প্রতি বছর ২৯ এপ্রিল এলে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ি।
এভাবে ভয়াল ২৯ এপ্রিলের ৩৪ বছর পার হলেও স্বজনহারার স্মৃতি আজও ভুলতে পারেনি চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চলের সাধারণ মানুষ। তাই প্রতি বছর ২৯ এপ্রিল এলে উপকূলীয় এলাকার মানুষের মধ্যে সেই স্বজনহারা স্মৃতিগুলো ভেসে ওঠে।
১৯৯১ সালের এদিনে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস তছনছ করে দিয়েছিল দেশের উপকূলীয় জনপদ। এদিন প্রায় ২৫০ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত এবং ৬ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস তছনছ করে দিয়েছিল উপকূলীয় জনপদ। সেদিনের ঘটনায় দেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ২ লাখ মানুষ প্রাণ হারান। সর্বস্ব হারায় প্রায় ১ কোটি মানুষ। ২৯ এপ্রিল মধ্যরাতে আঘাত হানা প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিল সীতাকু-ের সলিমপুর থেকে সৈয়দপুর পর্যন্ত ৯টি ইউনিয়ন। প্রায় ২২৫ কিলোমিটার গতিবেগ সম্পন্ন ও ৩০-৩৫ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসে উপকূল পরিণত হয়েছিল বিরাণ ভূমিতে। এ সময় মারা গিয়েছিল এলাকার প্রায় সাত হাজার মানুষ। আর নিখোঁজ হয়েছিল প্রায় তিন হাজার শিশু-নারী-পুরুষ। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল প্রায় তিনশ কোটি টাকার সম্পদ।
দেশে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড়গুলোর মধ্যে ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে নিহতের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের এই ঘূর্ণিঝড়ে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড, আনোয়ারা, বাঁশখালী, সন্দ্বীপসহ উরির চর ভোলাসহ বিভিন্ন এলাকায় অনেক মানুষ মারা যান।
২৯ এপ্রিলের সেই ধ্বংসযজ্ঞের স্মৃতি বয়ে উপকূলীয় মানুষের কাছে দিনটি ফিরে আসে বারবার। দিনটি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি শোকাবহ দিন। ১৯৯১ সালের এই দিনকে স্মরণ করে ঘূর্ণিঝড়ে নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় প্রতি বছর ২৯ এপ্রিল ঘরে ঘরে মিলাদ মাহফিল, কুরআনখানি, দোয়া কামনা, দুস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণসহ বিভিন্ন আয়োজনে দিনটি পালন করেন সীতাকুণ্ড, আনোয়ারা, বাঁশখালী, মহেশখালী, কুতুবদিয়াসহ সমগ্র উপকূল এলাকার মানুষ।
সীতাকুণ্ডের উপকূলবাসীর দিন কাটে আতঙ্কে
প্রকৃতিগতভাবে সমুদ্র ও পাহাড়বেষ্টিত হওয়ায় হাজার হাজার পরিবারের বসবাস সীতাকুণ্ডের সমুদ্র উপকূল ও পাহাড়ি এলাকায়। শিল্পাঞ্চলের খ্যাতিতে সমতলে আবাসন সঙ্কটের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বসবাসে বাধ্য হচ্ছে অসহায় পরিবারগুলো। নানা পরিকল্পনা হাতে নিয়ে পাহাড় ও উপকূল অঞ্চলকে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলা হলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে ঝুঁকিতে পড়ে প্রতি বছর জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বছর বছর ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের রক্ষায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিকল্পনা নেওয়া হলেও যথপোযুক্ত ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপের অভাবে রক্ষা হচ্ছে না জানমাল।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপজেলা পরিষদের অধীনে নামমাত্র দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ শত শত ভলান্টিয়াররা খাতা-কলমে নিয়োজিত থাকলেও থাকে না মাঠে-ময়দানে। যার ফলে দুর্যোগের ঘনঘটার সঙ্গে উপকূল ও পাহাড়ি এলাকাজুড়ে নেমে আসে চরম দুর্দশা। একজন কর্মকর্তা ও একজন অফিস সহকারীর অধীনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে ৬৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল। স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে পৌরসভা ও ৯টি ইউনিয়নে বিভিন্ন ইউনিটে ১ হাজার ১১০ স্বেচ্ছাসবী নিয়োজিত রয়েছে। নিয়ম মাসিক যেকোনো দুর্যোগে দায়ীত্বে কর্তব্যরত স্বেচ্ছাসেবক বা ভলান্টিয়াররা কাজ করার নির্দেশনা থাকলেও দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে কারো দেখা মেলে না বলে জানান স্থানীরা।
স্থানীয়রা বলেন, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ঝড়ের অবস্থা জানা সম্ভব হয়ে উঠে না। নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। ঘূর্ণিঝড়ে সব কিছু ভেসে যাওয়ার পর মাঝে মধ্যে দেখা যায় রেডক্রিসেন্টের পোশাক পরিধানকারী গুটি কয়েক লোকের। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার নির্দেশনা দিলেও পানীয় জল ও খাবারের ব্যবস্থা থাকে না বলে জানান তারা। নাম প্রকাশ না করা শর্তে এক ভলান্টিয়ার জানান, কোনো প্রকার বেতন-ভাতা না থাকায় দায়িত্ব পালনে অনিহা দেখান নিয়োজিত ভলান্টিয়াররা। বছরে কয়েকটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হলেও থাকে না ভাতা ও নাশতার ব্যবস্থা । বরাদ্দকৃত অর্থ কর্তাদের পকেটভারী হয়।। তড়িগড়ি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় । এ ছাড়া দুর্যোগ মোকাবিলায় উপকরণ জমে রয়েছে । এমন অনেক অভিযোগ। তা ছাড়া কর্তব্যরত কর্মকর্তার অনুপস্থিতির কারণে একজন অফিস সহকারী ও একজন পিয়নের মাধ্যমে চলে অফিসের কর্মকাণ্ড।
এ বিষয়ে উপজেলা রেডক্রিসেন্ট কর্মসূচি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যালয়ে উপপরিচালক হাফিজ আহাম্মদ বলেন, ‘বেতন-ভাতা ছাড়া স্বেচ্ছাশ্রমে কাজ করে ভলান্টিয়াররা। কাজের গতি আনতে হলে ভলান্টিয়ারদের কিছুটা ভাতার আওতায় আনা উচিত। বরাদ্দ না থাকায় প্রশিক্ষণের সুবিধা দেওয়া যায় না। অবশ্য উপকরণগুলো সকল ভলান্টিয়ারদের মাঝে বিতরণ করা হয় বলে জানান তিনি।
খালেদ / পোস্টকার্ড ;
সংবাদ শিরোনাম :
২৯ এপ্রিলের ভয়াল রাত
৩৪ বছর পরেও স্বজনহারা স্মৃতি ভুলতে পারেনি উপকূলবাসী, দিন কাটে আতঙ্কে
-
 মেজবাহ উদ্দীন খালেদ ।।
মেজবাহ উদ্দীন খালেদ ।। - আপডেটের সময় : ০১:৩০:১৯ পূর্বাহ্ন, মঙ্গলবার, ২৯ এপ্রিল ২০২৫
- ৩১ টাইম ভিউ
ট্যাগ:
২৯ এপ্রিলের ভয়াল রাত ৩৪ বছর পরেও স্বজনহারা স্মৃতি ভুলতে পারেনি উপকূলবাসী উপকূলবাসীর দিন কাটে আতঙ্কে
জনপ্রিয় পোস্ট